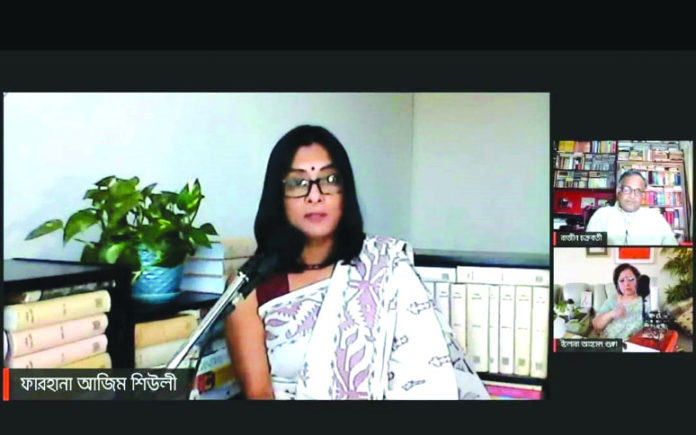ফারহানা আজিম শিউলী: টরন্টোভিত্তিক শিল্প-সাহিত্য চর্চার প্ল্যাটফর্ম ‘পাঠশালা’র ৩৯তম ভার্চুয়াল আসরটি অক্টোবর মাসের ২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অসামান্য সঙ্গীতস্রষ্টা-সঙ্গীতজ্ঞ অতুলপ্রসাদ সেন-এর সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিবেদিত পাঠশালার এ আসরে, পাহাড়ী সান্যালের লেখা ‘মানুষ অতুলপ্রসাদ’সহ আরও প্রাসঙ্গিক তথ্যের সমন্বয়ে সামগ্রিকভাবে অতুলপ্রসাদ সেনের জীবন ও সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করেন ভাষাবিজ্ঞানী-সঙ্গীত শিল্পী-সঙ্গীত সংগ্রাহক রাজীব চক্রবর্তী। অতুলপ্রসাদের গান পরিবেশন করেন অতুলপ্রসাদী গানের নন্দিত শিল্পী ইলোরা আহমেদ শুক্লা।
‘মোদের গরব, মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা!’
এই গানটি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, জড়িয়ে ছিল উপমহাদেশের স্বদেশী আন্দোলনেও। এই গান এখনো জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনে। এই প্রেরণা-জাগানিয়া গানটিসহ বাঙালি জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকা আরও অনেক গানের স্রষ্টা অতুলপ্রসাদ সেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে, ১৮৬১ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত কালপর্বে বাঙালি পেয়েছে চারজন কিংবদন্তি সুরসাধককে – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন এবং অতুলপ্রসাদ সেন। কাজী নজরুলের আগমন আরও প্রায় তিন দশক পরে। অতুলপ্রসাদ সেন বাংলা সাহিত্যের পঞ্চকবির (রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুল) একজন, বাংলা সঙ্গীতের প্রধান পাঁচজন স্থপতির একজন, পঞ্চ ভাস্করের একজন।
অতুলপ্রসাদ বাংলা গানে ঠুমরি ধারার প্রবর্তক। তিনি প্রথম বাংলায় গজল রচনাকারীদের অন্যতম একজন। সমকালীন গীতিকারদের তুলনায় তাঁর সঙ্গীত সংখ্যা সীমিত হলেও সাঙ্গীতিক মৌলিকত্ব দিয়ে তিনি বাংলা গানের ভুবনকে দিয়ে গেছেন অপার ঐশ্বর্য। তাঁর গানগুলো ‘গীতিগুঞ্জ’-তে সংকলিত আছে।
কেবল সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেই নয়- রাজনীতিবিদ, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষানুরাগী, সাহিত্য-সংগঠক, আইনজ্ঞ এবং সর্বোপরি একজন সংবেদনশীল মানুষ হিসেবেও বাঙালির কাছে অতুলপ্রসাদ সেন পরিচিত।

পাহাড়ী সান্যাল অভিনেতা হিসেবেই বঙ্গসমাজে বেশি পরিচিত। অথচ বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে চার দশকে তাঁর অভিনীত প্রায় সার্ধশত চলচ্চিত্রের অনেকগুলিতেই তিনি গায়ক-নায়ক। অতুলপ্রসাদের প্রত্যক্ষ শিষ্য পাহাড়ী অতুলপ্রসাদের গানকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদের গানের বেশির ভাগটাই রচিত হয়েছে লক্ষ্ণৌতে, তাঁর কর্মক্ষেত্রে, জীবনের শেষ বত্রিশ বছরে। আর সেই সময়টাতেই তাঁর খুব কাছাকাছি ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল। পাহাড়ী দীর্ঘদিন গান শিখেছেন অতুলপ্রসাদের কাছে। অতুলপ্রসাদকে, তাঁর নিঃসঙ্গ গান-জীবনকে অন্তরঙ্গে দেখেছিলেন পাহাড়ী সান্যাল। সেই দেখারই এক আশ্চর্য আখ্যান পাহাড়ী সান্যালের লেখা ‘মানুষ অতুলপ্রসাদ।’
পাহাড়ী সান্যাল ছাড়াও অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত ও জীবনের নানা দিক নিয়ে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্যে আসা দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অমল হোম, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তীসহ আরো অনেক গুণিজন। লিখেছেন অতুলপ্রসাদ নিজেও। সেসব সংকলিত আছে বিভিন্ন বইয়ে।

আসরের শুরুতেই শিল্পী ইলোরা আহমেদ শুক্লা পরিবেশন করেন মিশ্র কালাংড়া রাগে মানব পর্যায়ের অতুলপ্রসাদী গান – কে তুমি বসি নদীক‚লে একেলা। আলোচক রাজীব চক্রবর্তী এ গানের পেছনের গল্প অতুলপ্রসাদের নিজেরই একটা লেখা থেকে পড়ে শোনান। “একবার একটা কমিশনে যাচ্ছি গোমতী নদী দিয়ে নৌকো করে। মাঠের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়েছে নদীটা। বেশ মিঠে মিঠে হাওয়া বইছে। বসে বসে একটা বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছি। এমন সময় চোখে পড়ল অল্পবয়সের একটি মেয়ে নদীর একেবারে ধারে একলা বসে রয়েছে। কেমন যেন আনমনা হয়ে তাকিয়ে আছে। কিছুই যেন দেখছে না। হাওয়ায় চুলগুলি উড়ছে এলোমেলো। আধময়লা ঘাগড়াটাও উড়ছে এদিক সেদিক। কোনদিকেই ভ্রæক্ষেপ নেই মেয়েটির। দেখে মনটা যেন কেমন উদাস হয়ে গেল। উদাস করা একটা সুর মনে এসে গেল। তখনই এই গানটা লিখলাম।” শুক্লার দ্বিতীয় পরিবেশনা ছিল ভীমপলশ্রী রাগে ‘তুমি দাও গো দাও মোরে পরান ভরি দাও।’
রাজীব চক্রবর্তী বলেন, “আসলে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি অতুলপ্রসাদের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পেরিয়ে যাবার পরই করা। সার্ধশত বছরের উন্মাদনা যখন থাকে, তখন অনেক অনুষ্ঠান হয়। তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত কিছু থিতিয়ে পড়ে। আমরা একটু দেরি করেই এই অনুষ্ঠানটা করছি এইজন্য যে, অতুলপ্রসাদ নিয়ে চর্চা যেন থিতিয়ে না-পড়ে। আমরা সার্ধশতবর্ষের রেশটা ধরে রেখেই এই অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা করেছি। আপনারা জানেন, একটা বইকে কেন্দ্র করে পাঠশালার আসর হয়ে থাকে। মূলত আজ আমরা অতুলপ্রসাদের ওপর লেখা বিভিন্ন বই এবং অতুলপ্রসাদের নিজের নানা লেখা নিয়ে অতুলপ্রসাদ সম্পর্কিত আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব।” আমরা জানি, অতুলপ্রসাদ মানেই গান, গান এবং গান। সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় একটা সাক্ষাৎকারে অতুলপ্রসাদকে নিয়ে বলেছিলেন, ‘বাঙালি জাতি এই উপমহাদেশের অন্যান্য যে কোনো জাতির চেয়ে গানের ক্ষেত্রে একটু বেশি আবেগী।’ আর অতুলপ্রসাদকে নিয়ে যেখানে অনুষ্ঠান সেখানে গানের কথা বারবারই আসবে। আমরা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে অতুলপ্রসাদের গান মাঝে মাঝেই শুনে নেব। বিভিন্ন ধারার মিশ্রণ এসে ঘটেছে তাঁর গানের মধ্যে। সেগুলো আমরা নানাভাবে দেখে নেব, শুনে নেব। শুনে নেব রেকর্ডের গানও, পুরোনো রেকর্ডের গান। এর একটা কারণও আছে। কারণটা হচ্ছে, নজরুলকে নিয়ে যে ধরনের কাজকর্ম বাংলাদেশের নজরুল ইন্সটিটিউট করছে নজরুলের গানের স্বরলিপির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, অতুলপ্রসাদকে নিয়ে কিন্তু সে ধরনের কাজ হয়নি এই উপমহাদেশের কোথাও। অথচ অতুলপ্রসাদের সময়ের যাঁরা শিল্পী, যাঁরা অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে সরাসরি গান শিখেছেন, তাঁরা তাঁর সুরকে তাঁর কথাকে তাঁর ভাবভঙ্গিকে তাঁর গানের ধারাকে সার্বিক উপস্থাপনাতে তাঁদের মতো করে একটা ধারা তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেই ধারাটার সঙ্গে আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে যদি পরিচয় করাতে হয়, চিনিয়ে দিতে হয়, তাহলে আমাদের এই পুরোনো রেকর্ডিংগুলো বার বার ফিরে ফিরে শুনতে হবে। সেটা আমাদের পুরোনো রেকর্ডিং শোনানোর একটা অন্যতম উদ্দেশ্যও বটে।

“অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে কথা বলতে গেলে একটা কথা তো বলতেই হয়, অতুলপ্রসাদ তাঁর সমসাময়িক কালের আবিলতার মধ্যে থেকেই সেই আবিলতা পেরিয়ে গিয়েছিলেন। একজন বিশ্বমানের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। সেই মানুষ হয়ে ওঠার যে পথরেখা, সেই পথটা আজ আমরা দেখব। আমরা সেই পথের সহযাত্রী হব তাঁর সঙ্গে। আজকের আসরে আমরা অতুলপ্রসাদের জীবনকথা যেমন জানব, তেমনি তাঁর পড়াশুনার কথা, রাজনীতির কথা, তাঁর সার্বিক জীবনযাত্রার প্রসঙ্গও বারবার আসবে। ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর অতুলপ্রসাদের জন্ম ঢাকার লক্ষ্ণীবাজারে তাঁর মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তর বাড়িতে। কালীনারায়ণ বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রিক ব্রাহ্মসমাজের যে কাজকর্ম, আন্দোলনের সঙ্গে যে সমস্ত আয়োজন, তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। শুধু কালীনারায়ণ না, জড়িত ছিলেন অতুলপ্রসাদের বাবা রামপ্রসাদও। রামপ্রসাদ সেনের বাড়ি মাদারিপুরে। তিনি পড়াশুনা করতে কোলকাতায় এসেছিলেন। এসেই ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনি আকৃষ্ট হন এর প্রতি। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। লেখাপড়া করে ডাক্তার হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলন তাঁর জীবনে একটা অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল। তিনি ঢাকায় ফিরে গেলেন। বিয়ে করলেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরুষ কালীনারায়ণ গুপ্তর কন্যা হেমন্তশশীকে। ব্রাহ্ম সংস্কৃতির সঙ্গে এই ওতপ্রোত সম্পর্ক অতুলপ্রসাদকে একেবারে ছোটবেলা থেকে তাঁর মানসিক ক্ষেত্রটা গড়ে দিয়েছিল। অতুলপ্রসাদের বাবা গান গাইতেন। তিনিও বাবার সঙ্গে গাইতেন, পাখোয়াজ বাজাতেন, খোল বাজাতেন। একটা ব্যাপার আমরা জানি যে, ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের সমস্যা হয়েছিল সে সময়। কারণ হিন্দু সমাজ তাঁদেরকে ব্রাত্য করে রেখেছিল। ফলে হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের সঙ্গে তাঁদের আদানপ্রদান সেসময় খুব একটা ছিল না। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য কথা। বরং সমাজের তথাকথিত নিচু তলার মানুষ এবং মুসলমান জনসমাজের সঙ্গে তাঁদের আদানপ্রদান যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। রামপ্রসাদ ডাক্তার বলে সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে তাঁকে মিশতে হতো। ফলে রামপ্রসাদ সেনের ছেলে হিসেবে অতুলপ্রসাদের মানসিক ক্ষেত্রটা এই পারিবারিক আবহই তৈরি করে দিচ্ছিল। অতুলপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বৈষ্ণবদের গান শুনেছেন, প্রচুর পরিমাণে বাউলদের গান শুনেছেন। পরবর্তীকালে তিনি যে গানের সাম্রাজ্য তৈরি করবেন, গানের ইমারত-প্রাসাদ তৈরি করবেন, সেই প্রাসাদের উপকরণগুলি জুগিয়েছিল এই ছোটবেলার পরিবেশ।
“১৮৮৪ সালে অতুলপ্রসাদের মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর বাবা রামপ্রসাদ সেন মারা যান। ফলে হঠাৎ করে অতুলপ্রসাদ একেবারে তাঁর মাতামহের ওপর বা তাঁর মামাবাড়ির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তাঁর মাতামহ কালীনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মের প্রধান পুরুষ তো ছিলেনই, তিনি অসামান্য একজন গান রচয়িতাও ছিলেন। এই বিষয়গুলো ভীষণভাবে অতুলপ্রসাদের মনের ওপর ছাপ ফেলেছিল। তাঁর পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র সেন কবিরাজি করতেন। পিতৃব্য অর্থাৎ বাবার দাদা গুরুপ্রসাদ স্কুলে পড়াতেন। তাঁর ছেলে সত্যপ্রসাদ অতুলপ্রসাদের থেকে বয়সে অল্প একটু বড়ো ছিলেন। তিনি অতুলপ্রসাদের আবাল্য সঙ্গী এবং ঢাকাতে যতদিন রামপ্রসাদ বেঁচে ছিলেন, সত্যপ্রসাদ তাঁদের সঙ্গেই থাকতেন। রামপ্রসাদের মৃত্যুর পরে সত্যপ্রসাদ সহ অতুলপ্রসাদের পুরো পরিবার তাঁর মাতামহের বাড়িতে চলে যায়? তাঁর মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত, মাতামহী অন্নদা দেবী। আর তাঁর মাতুল কারা ছিলেন সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ অতুলপ্রসাদের পারিবারিক আবহ ছিল খুবই সম্বৃদ্ধ। আমরা জানি, ঢাকা অঞ্চলের যে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুদের বিশেষ একটা জাতিগোষ্ঠী বৈদ্য গোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাঁরা লেখাপড়ায় সংস্কৃতিতে ভীষণ উন্নত। ভীষণ একটা উঁচু স্তরে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। আমরা এও জানি যে, রামমোহনের সময় থেকে যে ব্রাহ্ম আন্দোলন শুরু হলো, যে সামাজিক আন্দোলন শুরু হলো, সেটি আমাদের বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম শিল্প সমস্তকিছুকে একটা অসম্ভব পরিশীলনের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল। এই পরিশীলিত সমাজের অন্তর্গত মানুষ ছিলেন অতুলপ্রসাদের মামার বাড়ির মানুষজন। তাঁর মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, বিখ্যাত স্যার কে জি গুপ্ত ছিলেন সিভিল সার্ভেন্ট। ডাঃ প্যারিমোহন গুপ্ত ছিলেন সিভিল সার্জন। তিনি বিলেতের শেফিল্ডে পড়াশোনা করেছেন। তিনি সাহানা দেবীর বাবা। ঘটনাক্রমে সাহানা দেবীরও খুব কম বয়সে বাবা প্যারিমোহন গুপ্ত মারা যান। তখন সাহানা দেবীরা চলে যান তাঁর মামার বাড়ি অর্থাৎ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতে। ফলে একদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, একদিকে প্যারিমোহন গুপ্ত, একদিকে কালীনারায়ণ গুপ্ত, একদিকে বাবা রামপ্রসাদ সেন এইরকম এক পরিবারে জন্মে অতুলপ্রসাদ বৃহত্তর সমাজ বৃহত্তর জীবনের খোঁজে বের হবেন পরবর্তীকালে, এটা আমরা বুঝতেই পেরেছিলাম। তাঁর অন্য মামা গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত ছিলেন অসামান্য সংস্কৃতিবান মানুষ, নাটক করতেন। আরেক মামা বিনয় চন্দ্র গুপ্ত। আর মায়ের সহোদরা ছিলেন সুবালা গুপ্ত। তিনি বয়সে অতুলপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ লিখেছেন। অন্য মাসিরা হলেন বিমলা, সৌদামিনী। আর ছোট মাসি সরলা দেবী হলেন সত্যজিৎ জনয়িত্রী সুপ্রভা রায়ের মা।। এই পারিবারিক আবহ অতুলপ্রসাদকে ভীষণভাবে অন্যতর অন্বেষণে পাঠিয়েছিল।

“সত্যপ্রসাদের ডায়রি অতুলপ্রসাদের জীবন সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। অতুলপ্রসাদকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি – একদম জন্ম থেকে বিলেত যাওয়া পর্যন্ত, প্রায় বিশ বছর ধরে। সত্যপ্রসাদের ডায়রি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জায়গা আমাদের অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে জানার জন্য।
“অতুলপ্রসাদের বাবা রামপ্রসাদ সেন, মা হেমন্তশশী। মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত। মামা স্যার কে জি গুপ্ত। এঁরই কন্যার সঙ্গে অতুলপ্রসাদ পরবর্তীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বাবার মৃত্যুর পর পরিপূর্ণভাবে কালীনারায়ণের অভিভাবকত্বেই অতুলপ্রসাদ বেড়ে ওঠেন। কালীনারায়ণ অসামান্য গায়ক এবং গীতিকার। ব্রাহ্মসমাজের গানের সংগ্রহের বই ‘ব্রহ্মসংগীত’-এ কালীনারায়ণের একাধিক গান স্থান পেয়েছে। কালীনারায়ণ অসাধারণ একজন পদ রচয়িতা, গান রচয়িতা। তাঁর ‘ভাব ও সংগীত’ বলে গানের বইও আছে। মামা গঙ্গাগোবিন্দ নাটকের মানুষ। মামার অভিনীত ‘শকুন্তলা’ নাটকের সুর অতুলপ্রসাদের মিশ্র কালাংড়া রাগে ‘বঁধু, ধরো ধরো মালা, পরো গলে’ গানটিতে এসেছে। মামার অভিনীত নাটকের সুর শুনে প্রভাবিত হয়ে অতুলপ্রসাদ সেই সুরে গানটি পরে তৈরি করেছিলেন। আর ১৪ বছর বয়সে বড় মামা কৃষ্ণগোবিন্দের কন্যা তপসীর অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে তিনি গান লিখেছিলেন বেহাগ-খাম্বাজে – তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া। এখনও এটি ব্রহ্মসঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হয়।
“এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ভারতীয় রাগ রাগিনীর সঙ্গেও ছোটবেলা থেকেই অতুলপ্রসাদের পরিচয় ঘটেছে সমান তালে। বাংলার বাউল কীর্তন এইসব গান শুনে তো বড়ো হয়েছেনই, তার সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদি গানও তিনি শিখেছেন, রপ্ত করেছেন, আয়ত্ত করেছেন, আত্মীকৃত করেছেন। ৬৩ বছরের জীবনে তিনি খুব বেশি লেখেননি। ‘গীতিগুঞ্জ’তে তাঁর যাবতীয় রচনা স্থান পেয়েছে বলে দাবি করা হয়। তবে এর বাইরেও কিছু রচনা থেকে যাওয়া অসম্ভব না। ‘গীতিগুঞ্জে’ ২০৮টি গান আছে। ২০৮টি গানের প্রায় প্রতিটিতেই রাগের নাম উল্লেখ করা আছে। এতে বোঝা যায়, ভারতীয় সঙ্গীত ধারার শিক্ষা তাঁর ছিল প্রথম থেকেই। সেই উত্তরাধিকার নিয়েই তিনি বেড়ে উঠছেন। বাউল ও কীর্তনের সুর শুনে তিনি যেমন বড়ো হচ্ছেন, তেমনি নি¤œবর্গের মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁদের সহজ সম্পর্ক এবং তখন পরাধীন দেশ। দেশপ্রেমের হাওয়া বইছে তখন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বসু এঁদের বক্তৃতা তিনি শুনছেন। একইসঙ্গে সংস্কৃতিতে যেমন তাঁর হাতেখড়ি হচ্ছে, তেমনি তিনি রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠছেন, দেশপ্রেমে দীক্ষিত হচ্ছেন। এইভাবে দীক্ষিত হতে হতে তাঁর মানসিক ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। প্রসঙ্গত কয়েকটি কথা এখানে বলে নেওয়া দরকার। ১৮৮৪ সালে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর তো তাঁরা এসে উঠলেন দাদুর বাড়িতে। তারপর অতুলপ্রসাদের জীবনে একটা দুর্ঘটনাই ঘটল বলা চলে। তাঁর মা হেমন্তশশী ১৮৯০ সালে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন। কোলকাতায় দাদা কৃষ্ণগোবিন্দের বাড়িতে তখন হেমন্তশশী থাকছিলেন। বিয়ে করলেন দুর্গামোহন দাশকে। দুর্গামোহন দাশ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যাঠামশাই। এই ঘটনাটি অতুলপ্রসাদকে খুব দুঃখ দিয়েছিল। তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন মায়ের এই আচরণে। এখনকার নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বলাই যেতে পারে, তাঁর মায়ের তো এই স্বাধীনতা ছিলই? কিন্তু সেই সময়, সেই অবস্থাটাকে বুঝতে হবে। সেইসময় মানসিকভাবে অতুলপ্রসাদ এই ঘটনাটা মেনে নিতে পারেননি। মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ একপ্রকার তিনি বন্ধই করে দিয়েছিলেন।

“ঢাকার পড়াশুনা শেষে কোলকাতা এসে অতুলপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। মা-দুর্গামোহনের সঙ্গে থাকতেন না তিনি, আলাদা থাকতেন। বোনেরা থাকতেন তাঁদের সঙ্গে? সেখান থেকে ব্যারিস্টারি পড়তে তিনি বিলেতে চলে যান ১৮৯০ সালে। ভেনিস হয়ে বিলেতে যাবার সময় ভেনিসের গন্ডোলা চালকদের গানের সুর শুনে সেই আদলে গান লেখেন – উঠ গো ভারত-লক্ষ্ণী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা। এই গানটির তৈরি হবার কাহিনি লিখেছেন অতুলপ্রসাদ – ‘ভেনিসে এক সন্ধ্যায় গন্ডোলা করে বেড়াচ্ছি। চারিদিকে বাড়ির আলো, আকাশের তারা, জলের ঝিকিমিকি, আর এধারে ওধারে গন্ডোলার ছপ ছপ ছপ শব্দ। চুপ করে দেখছি, শুনছি। হঠাৎ একটা গন্ডোলা থেকে সুর ভেসে এলো। বেহালা বাজাচ্ছে। চমৎকার লাগল সুরটা। গন্ডোলা দূরে চলে গেলেও সেই সুরটা কানে বাজতে লাগলো।’ এই গানটিই হচ্ছে ‘উঠ গো ভারত-লক্ষ্ণী।’ এই গানটি একসময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। এটি অতুলপ্রসাদের প্রথম জীবনের লেখা গান। এ পর্যায়ে রুমা গুহ ঠাকুরতার (ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার) গাওয়া এ গানটির রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়। উল্লেখ্য রুমা গুহ ঠাকুরতার সঙ্গে অতুলপ্রসাদের পারিবারিক যোগাযোগ আছে। রুমার মা সতী দেবী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ির।
“বিলেতে অতুলপ্রসাদ শ্রী অরবিন্দ, মনমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সরোজিনী নাইডুকে পেলেন, তাঁদের বন্ধু হলেন। এই বন্ধুত্ব তাঁকে স্বাধীনতার কথায়, দেশাত্মবোধে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল? পরবর্তীকালে সরোজিনী নাইডুর ভাই হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও অতুলপ্রসাদের চমৎকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়? সবাই মিলে বাংলা সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুললেন ‘স্টাডি সার্কেল,’ যার পুরোধা ছিলেন সাহিত্যিক এডমন্ড গস। এই পরিবেশ আবার তাঁর মধ্যে গানের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলল। এই সময়ে তিনি বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়ছেন, গানবাজনা শুনছেন – পৃথিবীর নানা ধরনের গানবাজনা, বিশেষত ইংরেজি গান শুনছেন। ম্যাডাম প্যাটের ‘হোম সুইট হোম’ গান শুনে ‘প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্’ এই গানটি লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, অতুলপ্রসাদের যে ২০৮টি গান ‘গীতিগুঞ্জে’ স্থান পেয়েছে, তার প্রত্যেকটার কিন্তু স্বরলিপি নেই, স্বরলিপি হয়নি। ব্রাহ্মসমাজ থেকে ‘কাকলি’ নামে তাঁর যে স্বরলিপির বই ৬টি খণ্ডে বেরিয়েছে, তাতে ১১৬টি গানের স্বরলিপি করা আছে। ‘প্রবাসী চল্ রে দেশে চল্’ গানটির স্বরলিপি কিন্তু এর মধ্যে নেই। ফলে অনেক গানেরই সুর আমরা জানি না।

“অতুলপ্রসাদ বিলেতে গান শুনলেন, বিভিন্নরকম সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হলেন, ব্যারিস্টার হলেন, ফিরে এলেন কোলকাতায়। এসে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিং এর অধীনে কাজ শুরু করলেন। ওকালতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো নানারকম কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কোলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তাঁকে ঘিরে ধরল, ছেঁকে ধরল একেবারে। তিনি ১৮৯৬ সালে ‘খামখেয়ালী সভা’র সভ্য হলেন। এটি রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তৈরি একটি সাহিত্য ও সঙ্গীত মণ্ডলী। নাম থেকেই বোঝা যায় এর কোনো নির্দিষ্ট বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এর সদস্যরা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজা জগদীন্দ্র নারায়ণ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন পালিত এরকম সব মানুষেরা। আর এ সভার কার্যপ্রণালীতে ছিল হাস্যরসের উদ্দীপনা করা, সাহিত্যকে আনন্দে সরস করা, নানাবিধ সঙ্গীতের দ্বারা সভ্যদের চিত্ত আকৃষ্ট করা এবং সভান্তে জঠরের সম্যক তুষ্টি সাধন? এই সভার একটা নিয়ম ছিল, প্রতি সভায় প্রত্যেক বিদেশি শব্দের জন্য এক আনা জরিমানা ধার্য। এইরকম একটা উদ্ভট সভার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন অতুলপ্রসাদ। দিলীপকুমার রায় তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, ‘তাঁর ভেতরের বাদী সুর হচ্ছে সবসময় প্রেম।’ যেখানেই তিনি আড্ডা পেয়েছেন, যেখানেই বন্ধুদের সাহচর্য পেয়েছেন, সেখানেই তিনি মজে গেছেন। ‘খামখেয়ালী সভা’য় মজে যাওয়ার কারণ কিন্তু অতুলপ্রসাদের এই স্বভাব। এর সূত্র ধরেই দেখব, এরপরে যখন লক্ষ্ণৌ থেকে মাঝখানে একবার ফিরে আসছেন কোলকাতায় বিশেষ কারণে, তখন সুকুমার রায়ের ‘মনডে ক্লাব’ বা ‘মণ্ডা ক্লাবে’র সদস্য হচ্ছেন তিনি। ‘ননসেন্স ক্লাব’ যাকে নাম দিয়েছিলেন সুকুমার রায়। ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে তৈরি হয়েছিল এটি। সেইখানে অঅতুলপ্রসাদ সদস্য হয়ে পড়লেন। সেখানের সদস্য ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুকুমার রায়, গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, কালিদাস নাগ, শ্রীশচন্দ্র সেন, অমল হোম, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অর্থাৎ তখনকার কোলকাতার শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, শিক্ষিত মানুষেরা সব এই ক্লাবের সদস্য। সেখানে এসে পড়লেন অতুলপ্রসাদ এবং খুব সহজেই সেই ক্লাবের এক উৎসাহী সদস্য হয়ে পড়লেন। সেখানে গানবাজনা তো চলতো, তার সঙ্গে চলতো আড্ডা। ‘মনডে ক্লাবে’র জন্য একটি মজাদার গানও লিখেছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। গানটি হচ্ছে – ‘আমাদের শান্তিনিকেতন। আরে না, তা না আমাদের মনডে সম্মিলন। আমাদের হল্লারই কুপন। তার উড়োচিঠির তাড়া মোদের ঘোরায় পাড়া পাড়া। কভু পশুশালে হাসপাতালে আজব আমন্ত্রণ।’ এ পর্যায়ে মানডে ক্লাবের সভ্যদের একটি ঐতিহাসিক স্থিরচিত্র দেখানো হয়। এতে আছেন সুবিনয় রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অতুলপ্রসাদ সেন, শিশিরকুমার দত্ত, সুকুমার রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমল হোম, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, হীরেন সান্যাল, অজিতকুমার চক্রবর্তী, কালিদাস নাগ, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিরিষচন্দ্র সেন ও গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।
“অতুলপ্রসাদের জীবনের কথা বলতে গিয়ে আমরা তাঁর মনের গতিপথ দেখার চেষ্টা করছি। সেই গতিপথে দেখতে পাচ্ছি, তিনি সবসময় নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে এবং মজা-আড্ডা এসবের মধ্যে আছেন, সবসময় তিনি এসবের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন।”

এ পর্যায়ে ইলোরা আহমেদ শুক্লা পরিবেশন করেন মিশ্র আশাবরী রাগে দেবতা পর্যায়ের অতুলপ্রসাদের গান – ওগো নিঠুর দরদী, এ কি খেলছ অনুক্ষণ। এটি একটি ঠুমরি। মানসী মুখোপাধ্যায় লিখছেন, “টপ্পার সুরে গান রচনার দক্ষতা অতুলপ্রসাদের পূর্বে নিধুবাবু দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদের কৃতিত্ব হল মিশ্র টপ্পার সুরে বাংলা গান পরিবেশনে। যেমন, টপ্পা ও ঠুংরির মিশ্রিত সুরে ‘ওগো নিঠুর দরদী,’ ‘কে গো তুমি বিরহিনী’ ইত্যাদি।” রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখছেন, “১৯২৩ এ রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার এলেন লক্ষ্ণৌতে, অতুলপ্রসাদের বাড়িতে। খবর পেয়ে হঠাৎই এসে পড়লেন হেমকুসুমও। দুজনে সঙ্গ দিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তারপর রবীন্দ্রনাথের যাওয়ার দিন ছেলেকে নিয়ে হেমকুসুমও ফিরে গেলেন ক্যান্টনমেন্ট রোডের বাড়িতে। সেদিন সন্ধ্যায় অতুলপ্রসাদ লিখলেন, ‘ওগো নিঠুর দরদী, এ কী খেলছ অনুক্ষণ? তোমার কাঁটায় ভরা বন তোমার প্রেমে ভরা মন/ মিছে দাও কাঁটার ব্যথা, সহিতে না পার তা/ আমার আঁখিজল তোমায় করে গো চঞ্চল।” শুক্লার চতুর্থ পরিবেশনা ছিল আশাবরী রাগে মানব পর্যায়ের – মুরলী কাঁদে রাধে রাধে ব’লে। গানটি আশাবরীতে হলেও এতে ভৈরবী আছে। শুদ্ধ নিষাদ ও ধৈবতও এসেছে চমৎকারভাবে গানটিতে। এ পর্যায়ে ঠুমরি প্রসঙ্গে পুনার হরিকৃষ্ণ মন্দিরে দিলীপকুমার রায়ের অতুলপ্রসাদকে নিয়ে বক্তৃতার অডিও বাজিয়ে শোনানো হয়। রাজীব অডিও-ভাষ্যের মূলবক্তব্য সম্পর্কে বলেন, “বাংলা গানে ঠুমরির প্রচলন করেন অতুলপ্রসাদ। রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল ধ্রæপদ ও খেয়ালকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ঠুমরির চল বাংলা গানে প্রথম অতুলপ্রসাদ করেন। দিলীপকুমার রায়ের বক্তব্য হচ্ছে, এই যে চলনটা অতুলপ্রসাদ প্রচলন করলেন, রাসায়নিক ভাষায় বলতে গেলে এটা কম্পাউন্ড, মিক্সচার নয়। এমন নয় যে বাংলার সঙ্গে স্রেফ হিন্দি সুরের ধারাটা মিশিয়ে একটা জগাখিচুরি কিছু তৈরি করলেন, তিনি বরং একটা নতুন রুপ দিলেন, বাংলার একটা নিজস্ব ঘরানা তৈরি করলেন। এবং এটিই অতুলপ্রসাদের বিশেষত্ব। তিনি শুধুমাত্র নতুন একটা কিছু করতে হবে বলে করলেন না। দিলীপ রায় বলেছেন, ‘শিল্পে আমরা পুনরাবৃত্তি চাই না, চাই নতুন সৃষ্টি।’ অতুলপ্রসাদ ঠুমরিটা নতুন করে তৈরি করলেন।
“গজল প্রসঙ্গে বলতে হয়, অতুলপ্রসাদ গজল লিখেছেন কিন্তু বাংলায় গজলের তিনি উদগাতা নন। তিনি গজলের ধারা পেয়েছেন দিলীপ রায়ের কাছ থেকে। এ প্রসঙ্গে দিলীপ রায়ের নিজস্ব লেখাই আছে। ১৯২২-২৩ এ অতুলপ্রসাদ গজল শুনেছেন দিলীপ রায়ের কাছে এবং সেই গজল শুনে তিনি নিজে একটি গান রচনা করেছেন – কত গান তো হল গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও?” এ গানটি তৈরির পেছনের গল্প নিয়ে ‘মানুষ অতুলপ্রসাদ’ বইয়ে পাহাড়ী সান্যাল লিখছেন – “আমি তখন ইন্টার-মিডিয়েট পড়ি। সেই সময় একবার মন্টুদা (দিলীপকুমার রায়) লক্ষ্ণৌতে এল এবং তাঁর নিজের রচিত একটি গান যেটির প্রথম ছত্র হল – ‘যদি দিন না দেবে তবে এত ব্যথা কেন সওয়াও’ – এই গানখানি আমাকে খুব যতœ করে শেখালো। আমার অসম্ভব ভাল লাগল শিখতে এবং শিখে আমি অতুলদার কাছে গানখানি গাইলাম। মন্টুদাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।ৃ অতুলদা চোখে চশমা এঁটে তাঁর লেখা গানখানি পড়ে শোনালেন। অতুলদা গানের প্রথম ছত্রটি যখন গাইলেন তখন আমি হঠাৎ হারমোনিয়াম থামিয়ে বলে উঠলাম, ‘এ কী অতুলদা! এ যে মন্টুদার ‘যদি দিন না দেবে’র সুর!… কালক্রমে মানুষের মন থেকে মন্টুদার লেখা ও গাওয়া ‘যদি দিন না দেবে’ গানখানি মুছে গেল। আর মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে বেঁচে রইল অতুলপ্রসাদের ‘কত গান তো হল গাওয়া।’ এই গানখানি সাহানা দেবী তাঁর রেকর্ডের মাধ্যমে অদ্ভুত সুন্দরভাবে প্রচার করেছেন মানুষের কাছে।” এ পর্যায়ে ‘কত গান তো হল গাওয়া’ সাহানা দেবীর কণ্ঠেই রেকর্ড থেকে বাজিয়ে শোনানো হয়।
রাজীব বলেন, “একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের গানে সুবিধে হচ্ছে, নানাভাবে তার ডক্যুমেন্টেশন হয়েছে। গানগুলোর স্বরলিপি তৈরি হয়েছে, পর্ব বিভাগ হয়েছে, পর্যায় বিভাগ হয়েছে। অতুলপ্রসাদের গানে কিন্তু এত সুযোগ হয়নি। কারণ অতুলপ্রসাদ নিজে অল্পকিছু করে গিয়েছিলেন, আর তাঁর সময়ের মানুষের মধ্যে সাহানা দেবী কিছু করেছেন, দিলীপকুমার রায় কিছু করেছেন। তারপরে তাঁর গানের প্রকৃষ্টভাবে রক্ষণাবেক্ষণে আর উৎসাহী হইনি আমরা। এমনকি সুর নিয়েও নানা রকমের ব্যভিচার অতুলপ্রসাদের গানে চলেছে। অতুলপ্রসাদের গানের বই ‘গীতিগুঞ্জ’র গানগুলিকে তিনি ৫টা ভাগে ভাগ করেছেন। ভাগগুলো হচ্ছে – দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব এবং বিবিধ। ‘গীতিগুঞ্জ’ বের হবার আগে ‘কয়েকটি গান’ বলে একটি সংকলন বেরিয়েছিল অতুলপ্রসাদের গানের। ১৪৭টি গান সেই সংকলনে স্থান পেয়েছিল। সেখানে বিভাগটা একটু অন্যরকম ছিল – দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব এবং ছয় রাগ ও ছয় ঋতু। মডার্ন আর্ট প্রেস থেকে বইটি বেরিয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯২৩ সালের মার্চে রবীন্দ্রনাথ আসেন লক্ষ্ণৌয়। সেসময় অতুলপ্রসাদের রচিত গান ‘কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা’ শ্রোতারা রবীন্দ্রনাথের গান বলে ভাবেন। সে কথা জেনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুরোধ করেন, শীঘ্রই যেন অতুল নিজের রচিত গানের একটি বই প্রকাশ করেন। এর দুবছর পর ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় ‘কয়েকটি গান।’ আর ১৯২৯-৩০ এ বেরিয়েছিল ‘কাকলি’র ১ম ও ২য় ভাগ। একবার অতুলপ্রসাদ কোলকাত যাওয়ার সময়ে হাওড়া স্টেশনে নেমেই বেশ কিছু ছেলেকে তাঁরই লেখা স্বদেশী গান গাইতে শুনেছেন। একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘এ গান কার লেখা, ভাই?’ সে উত্তর দিয়েছিল, ‘কেন, এ তো অতুলপ্রসাদ সেনের, আপনি জানেন না?’ অর্থাৎ তাঁর গান লোকের মুখে মুখে ফিরলেও তাঁকে অনেকেই চিনত না। ১৯২৫ সালটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সালেই ‘প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে’র মুখপাত্র অসামান্য সাহিত্য পত্রিকা ‘উত্তরা’র সফল আত্মপ্রকাশ হয়। ‘উত্তরা’ নামকরণটি অতুলপ্রসাদের। তিনি ‘প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন’ ও ‘উত্তরা’র অন্যতম উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। আবার এই ১৯২৫ সালেই অতুলপ্রসাদের গানের প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড বের হয়। সাহানা দেবী প্রথম গান করেন।” এ পর্যায়ে সাহানা দেবীর কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের কাছে দার্জিলিঙে সাহানার বড়ো মেসোমশাই ডাঃ পি কে রায়ের বাড়িতে প্রথম শেখা গান মিশ্র কালাংড়া রাগে ‘বঁধু, ধরো ধরো মালা পরো গলে’র খানিকটা বাজিয়ে শোনানো হয়।

শুক্লার পঞ্চম পরিবেশনা ছিল – আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার। গানটি দেবতা পর্যায়ের, মিশ্র খাম্বাজ রাগে। খাম্বাজ ছিল অতুলপ্রসাদের সবচেয়ে প্রিয় রাগ। মিশ্র খাম্বাজ, গুজরাটি খাম্বাজ, সিন্ধু খাম্বাজ, বেহাগ খাম্বাজ, ঝিঁঝিট খাম্বাজ, পিলু খাম্বাজ – সব ধরনের খাম্বাজেই তিনি গান বেঁধেছেন। মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে, যাব না যাব না যাব না ঘরে, জয়তু জয়তু জয়তু কবি – এ গানগুলো নটমল্লার রাগে হলেও প্রধানত খাম্বাজেরই চলন দেখা যায়। কবির রচিত প্রথম গান ‘তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে’ও বেহাগ-খাম্বাজে। রাজীব বলেন, “’গীতিগুঞ্জে’ অতুলপ্রসাদের ২০৮টি গানে ৮০ রকমের রাগ ও সুরের বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোথাও রাগের উল্লেখ রয়েছে, কোথাও রয়েছে বাউল কীর্তন এসব লেখা। বেশ কিছু অপ্রচলিত রাগেও গান আছে যেমন জয়শ্রী, খট, মেঘ, পঞ্চম, নট-নারায়ণ, নায়কী, কানাড়া, কর্ণাটী ইত্যাদি।”
এরপর শুক্লা অতুলপ্রসাদের স্বদেশ পর্যায়ের বেহাগ রাগে ‘আপন কাজে অচল হলে চলবে না রে চলবে না’ গানটি গেয়ে শোনান। এ পর্যায়ে বেহাগ রাগেই দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের গান ‘তুমি গাও তুমি গাও গো’ রেকর্ড থেকে বাজিয়ে শোনানো হয়। রাজীব বলেন, “অতুলপ্রসাদী গানের গায়কি সম্পর্কে জানতে হলে এই গানগুলোর কাছে আমাদের বারবার ফিরে যেতে হবে। আরেকটি জরুরি কথা হচ্ছে, অতুলপ্রসাদের গানের আলোচনায় তাঁর গানের স্বরলিপিকারদের কথা বরাবরই উপেক্ষিত, কখনোই তাঁদের কথা আসে না। দিলীপকুমারের গাওয়া গানটির স্বরলিপিকার হরিপদ রায়। হরিপদ রায় বিখ্যাত গায়ক। তাঁর প্রচুর রেকর্ড বেরিয়েছিল একসময়। অতুলপ্রসাদের গানও তিনি গেয়েছেন। অতুলপ্রসাদের গানের সবচেয়ে বেশি স্বরলিপি করেছেন সাহানা দেবী। ‘কাকলি’র প্রথম দুটো খণ্ডের গানগুলোর স্বরলিপিকার হিসেবে সাহানা দেবীর নাম আছে। এছাড়া দিলীপকুমার রায়, রবীন্দ্রমোহন বসু স্বরলিপি করেছেন। রবীন্দ্রমোহন বসু সে আমলের একজন বিখ্যাত গায়ক, রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড তাঁর আছে, অতুলপ্রসাদের গান গেয়েছেন। স্বরলিপি আরো করেছেন অনিল হোম, বিষ্ণুপুরের সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, নীহার বিন্দু সেন। নীহার বিন্দু সেন প্রচুর গানের স্বরলিপি করেছেন মূলত রেনুকা দাশগুপ্তর গান শুনে। অতুলপ্রসাদের গানের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এঁদের নামগুলি উল্লেখ করা দরকার, এঁদেরকে নিয়ে আমাদের জানা দরকার, এঁদের নিয়ে আলোচনা করা দরকার। আরো আছেন বিখ্যাত সঙ্গীত পণ্ডিত রাজ্যেশ্বর মিত্র। আরেকটা নাম অতুলপ্রসাদের স্বরলিপিকার হিসেবে উল্লেখ করতে হয়। আমরা অনেকে জানিই না যে, অতুলপ্রসাদের সঙ্গে এই মানুষটির সংযোগ তৈরি হয়েছিল। তাঁর নাম সুরসাগর হিমাংশু কুমার দত্ত। হিমাংশু দত্ত অতুলপ্রসাদের অন্তত ৩-৪টি গানের স্বরলিপি তো করেছেনই। এছাড়া অতুলপ্রসাদ বাংলা গানের পাশাপাশি একটিমাত্র ব্রজবুলিতে গান লিখেছিলেন – আজি হরষ সরসি কি জোয়ারা। এই গানের স্বরলিপি করেছেন স্নেহ দাস নামে এক ভদ্রমহিলা। তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের ভুবনডাঙার বাসিন্দা। ১৯২০ এর দশকের কোনো এক সময়ে এই গানটি তিনি শিখেছিলেন। শেখা গানের স্মৃতি থেকে এর প্রায় ৫০-৬০ বছর পরে তিনি গানটির স্বরলিপি তৈরি করেন।” এ পর্যায়ে স্বরলিপিকার হরিপদ রায়ের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের ‘মনোপথে এলো বনহরিণী একি মনোহারিণী’ গানটি পুরোনো রেকর্ড থেকে বাজিয়ে শোনানো হয়। রাজীব বলেন, “যেহেতু হরিপদ অতুলপ্রসাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন, তাই তাঁর গাওয়া গানের একটা আলাদা মূল্য আছে।

“আবার অতুলপ্রসাদের জীবনে ফিরে যাই। অতুলপ্রসাদ কোলকাতায় ফিরলেন।
সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিং এর অধীনে কাজ করা শুরু করলেন, ‘খামখেয়ালী সভা’র সদস্য হলেন। এইসময় অতুলপ্রসাদের জীবনে একটা অন্যরকম ঘটনা ঘটে গেল। বিলেতে যখন তিনি ছিলেন, তখন তাঁর মামা স্যার কে জি গুপ্তও বিলেতে। কে জি গুপ্তর কন্যা হেমকুসুমের সঙ্গে তখন অতুলপ্রসাদের সখ্য গড়ে ওঠে। আসলে মা’র দ্বিতীয়বার বিয়ের সময় থেকে অতুলপ্রসাদ ভেতরে ভেতরে একটু একা। সেই একাকীত্বে মনে হয় তিনি একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন হেমকুসুমের মধ্যে। হেমকুসুম শিক্ষিত, গুণি, এস্রাজ বাজাতে পারতেন, গান গাইতেন, কাব্যানুরাগী ছিলেন। আমরা পরবর্তীতকালেও দেখব যে, অতুলপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর যৌথজীবন নানাভাবে বিঘিœত হয়েছে, ব্যক্তিত্বের সংঘাত হয়েছে, তবুও হেমকুসুম সারাজীবন অতুলপ্রসাদের গান গেয়েছেন। অতুলপ্রসাদের সঙ্গে একসময় তাঁর মুখ দেখাদেখি প্রায় ছিল না। কিন্তু অতুলপ্রসাদের গান তিনি সবসময় গাইতেন। এই হেমকুসুমের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের সম্পর্কটা গড়ে ওঠে বিলেতে থাকার সময়। অতুলপ্রসাদ বিলেত থেকে ফিরে এসে ভাগ্যের অন্বেষণে কাজ শুরু করলেন। কোলকাতায় ততটা সাফল্য এলো না। তিনি চলে গেলেন রংপুরের দিকে একবার। চেষ্টা করলেন কিছুদিন কাজ করতে সেখানে। তাতেও খুব একটা সাফল্য আসেনি। তার মাঝখানে বিয়েও করলেন ১৯০০ সালে, বিলেতে। সন্তান হলো ১৯০২ সালে বিলেতে, জমজ সন্তান – দিলীপকুমার ও নিলীপকুমার। ৭ মাস বয়সী নিলীপকুমারের মৃত্যুও হয় বিলেতে, সমাধিও বিলেতে। তখন বিলেতেও অতুলপ্রসাদ বৃত্তিতে খুব একটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। আমরা জানি তার আগে অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের বিয়েতে তাঁদেরকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মস্ত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভারতবর্ষে তখন মাসতুতো-পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ের চল ছিল না। তাই তাঁদেরকে স্কটল্যান্ডে গিয়ে বিয়ে করতে হয়। এসব ঘটনা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এসব পরে তাঁর জীবনকে নানানভাবে ব্যতিব্যস্ত করবে। বিলেত থেকে কোলকাতায় ফিরে বন্ধুদের পরামর্শে তিনি চলে গেলেন লক্ষ্ণৌতে ১৯০২ সালে।” এ পর্যায়ে অতুলপ্রসাদের পরিবারের সদস্যদের স্থিরচিত্র দেখানো হয়।
রাজীব বলেন, “১৯০২ থেকে ১৯৩৪ এই ৩২ বছর অতুলপ্রসাদ মূলত লক্ষ্ণৌতে কাটিয়েছেন। তিনি এদিক ওদিক গেছেন, কোলকাতায় ফিরে এসেছেন মাঝখানে ১৯১৬ সালের শুরুতে। ১৯১৫ সালের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত ‘মনডে ক্লাব’ এর সদস্য হলেন। কিন্তু মূলত লক্ষ্ণৌকেন্দ্রিক জীবনই ছিল তাঁর। লক্ষ্ণৌতে যখন গেলেন, তখন তাঁর এতদিনের শিক্ষা, সাঙ্গীতিক দীক্ষার সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ের উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের নিবিড় পরিচয় শুরু হলো। এর ফলে তিনি যে গজল, ঠুমরি এসব আঙ্গিক নিয়ে কাজ করেছেন সেসবের সুরের গ্রহিষ্ণুতা তৈরি হয়েছিল তাঁর। লক্ষ্ণৌয়ে তাঁর বাড়িটা ছিল শিল্প-সংস্কৃতির একটা এপিসেন্টার। তাঁর বাড়িতে কে না আসতেন? বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অতুলপ্রসাদের লক্ষ্ণৌয়ের বাড়ির এক গানের জলসা নিয়ে লিখছেন, ‘লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হবার পর কয়েকজন বাঙালি প্রফেসর সেন মহাশয়ের সন্ধ্যার সঙ্গী হলেন নিয়মিতভাবে। কিন্তু তার আগে অতুলপ্রসাদের কেশরবাগের বাড়িতে মজলিশ বসত সময় সময় বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যে। শুনেছি সেগুলোতে উপস্থিত থাকতেন সত্যকুমার মুখার্জি, নির্মল দে, বিজন ব্যানার্জি, শম্ভু চৌধুরী, শৈলেন সান্যাল, দ্বিজেন সান্যাল। এঁদের মধ্যে দ্বিজেন সান্যাল ও পাহাড়ী সান্যাল ভাল গাইতেন এবং অতুলপ্রসাদের প্রতি এবং তাঁর গানের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ৃলক্ষ্ণৌতে প্রায় প্রতি রোববারই ছোটখাট বৈঠক হত। সেটা আসলে ঘরোয়া বৈঠক। বেশ বড় জলসা বছরে তিন চারবার হত এবং সেগুলি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বৈঠক। যখন কোনো বিখ্যাত গাইয়ে হয় রামপুর অথবা গোয়ালিয়র থেকে অথবা হায়দ্রাবাদ মথুরা ইন্দোর কাশী কোলকাতা থেকে আসতেন অথবা আবদুল করিম আসতেন তখন সেন মহাশয়ের বাড়িতেই একটা বৈঠক হত। কখনো কখনো ভাতখণ্ডেজিকে পেয়েছি, শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকারকেতো সর্বদাই পেয়েছি। বাইরে থেকে আসা ওস্তাদদের বৈঠকে সেন মহাশয়ের বেশ খরচ হত। কখনও কখনও অন্যত্রও জলসা হত যেমন রাজা নবাব আলির বাড়ি, সেলিমপুরের বাড়ি, রাজেশ্বর ও উমানাথ পালির বাড়ি অথবা অন্য কোনো সঙ্গীতরসিকের বাড়ি। এক রবিবার সকালে একটি বড় আসর বসবে বলে জানাল। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণখুলে একটি গানই চল্লিশ মিনিট গাইলেন – ভবানী দয়ানী। সকলের মন ভরে গেল। আরও দুতিনখানা ছোট গান হল। দুঘণ্টার ওপর সময় কাটল। চমৎকার লাগল। পরেরদিন সন্ধ্যেবেলা আমি আর ধূর্জটি বাবু (ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) ধীরে ধীরে সেন মহাশয়ের কক্ষে প্রবেশ করলাম। তিনি বিশেষ আনন্দে স্বাগত জানালেন এবং তারপর শোনালেন যে গানটি তিনি সদ্য লিখেছেন ভবানী দয়ানীর অনুকরণে।’ ভবানী দয়ানীর সুরে বাঁধা সেই গানটি হলো – সে ডাকে আমারে বিনা সে সখারে রহিতে মন নারে। ‘ভবানী দয়ানী’ ভৈরবীতে রচিত একটি সাদরা।” এ পর্যায়ে পারভিন সুলতানার কণ্ঠে রেকর্ড থেকে বাজিয়ে ‘ভবানী দয়ানী’ গানটি শোনানো হয়। রাজীব বলেন, “‘সে ডাকে আমারে’ গানটি ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ চলচ্চিত্রে পাহাড়ী সান্যালকে দিয়ে গাইয়েছেন সত্যজিৎ রায় স্বয়ং।” শুক্লা এ গানের কিছু অংশ গেয়ে শোনান শ্রোতা-দর্শকের অনুরোধে।

এ পর্যায়ে পাহাড়ী সান্যালের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের ‘যাব না, যাব না, যাব না ঘরে’ গানটির একটি প্রাইভেট রেকর্ডিং বাজিয়ে শোনানো হয়। এরপর একই গান সাহানা দেবীর কণ্ঠে বাজিয়ে শোনানো হয়। এ গান লেখার পেছনের গল্প নিয়ে আশিস পাঠক লিখছেন, “এর পরই সেই চরম বিচ্ছেদের দিন। এক বন্ধুর জন্মদিনের উৎসব থেকে ফিরে অতুলপ্রসাদ দেখলেন তাঁর সমস্ত পোশাক-আসাক আগুনে পোড়াচ্ছেন হেমকুসুম। সেদিন আর বাড়িতে ঢোকেননি অতুলপ্রসাদ। পরের দিনই কলকাতায় এসে ওঠেন জ্যাঠতুতো দাদা সত্যপ্রসাদের বাড়িতে। সত্যপ্রসাদ ডায়েরিতে লিখেছেন, ‘অতুল আমার বুকে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত। নীরবতার মধ্যেই তাহার প্রাণের বেদনা জানিতে ও বুঝিতে পারিতাম। এরূপ সমবেদনায় আমরা কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছি। সেবারেই অতুল তাঁর গানটি রচনা করে – যাব না, যাব না, যাব না ঘরে, বাহির করেছে পাগল মোরে।’”
পাহাড়ী সান্যাল এই গানটি শেখেন স্বয়ং অতুলপ্রসাদের কাছে। এই গান শেখার অভিজ্ঞতা পাহাড়ী বিশদভাবে লিখেছেন তাঁর লেখা ‘মানুষ অতুলপ্রসাদ’ বইয়ে। এই গানে দাম্পত্যের যে দ্ব›দ্ব সংঘাত আছে সেসবের সামনে দাঁড়িয়ে অতুলপ্রসাদ মানুষটি কেমন ছিলেন তাও লিখেছেন পাহাড়ী সান্যাল। “আমার অতুলদা ছিলেন আশাবাদী মানুষ। যখন তিনি প্রগাঢ় বেদনা গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন তখনও তার মধ্যে তিনি কোনদিন আশাকে ছাড়েননি। যার জন্যেই তিনি বলতে পেরেছেন, ‘দুঃখেরে আমি ডরিব না আর, কণ্টক হোক কণ্ঠের হার, জানি তুমি মোরে করিবে অমল, যতই অনলে দহিবে।’ দুঃখের মধ্যেও, ব্যথার মধ্যেও, প্রেমের ব্যথার মধ্যেও তাঁর নিবিড় আগ্রহ তিনি কোনদিন বর্জন করতে পারেননি। তার কারণ অতুলদা ছিলেন সত্যিকারের প্রেমিক। প্রেম তাঁর কাছে ছিল ভগবানের প্রতীক। একজন মানুষ যে এতভাবে ভালবাসতে পারেন তা যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্টভাবে দেখেছেন তাঁরাই বুঝতে পেরেছেন।”

শুক্লার সপ্তম পরিবেশনা ছিল পিলু বারোয়াঁ রাগে মানব পর্যায়ের ‘কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে।’ রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখছেন, “উত্তর ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের আঙ্গিকে অতুলপ্রসাদের কয়েকটি গান শুনলে অনেকটা ধুন মনে হবে। যেমন পিলু বাঁরোয়ায় কে আবার বাজায় বাঁশি ইত্যাদি।” ১৯৩৪ সালে অতুলপ্রসাদ হাওয়া বদলের জন্য পুরীতে যখন যান, তখন মহাত্মা গান্ধীও পুরী এসেছিলেন। অতুলের কাছে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার মানুষ। তাঁর অনুরোধে অতুল গান্ধীজীর প্রিয় গান ‘কে আবার বাজায় বাঁশি’র হিন্দী অনুবাদ করে শোনান। গান্ধীজী মুগ্ধ হন ও তাঁর গানের অজস্র প্রশংসা করেন। এরপর কাজরী ঢং এ বাঁধা ‘জল বলে চল মোর সাথে চল’ গেয়ে শোনান শুক্লা। রাজ্যেশ্বর মিত্র এ গানটি সম্পর্কে বলেছেন, এটি শুনলেও ধুন মনে হবে। রণজিৎ সেনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অতুলপ্রসাদ জানিয়েছিলেন, গান বাঁধবার জন্য তাঁর কখনও বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন পড়ত না। রিসেস এর সময়ে কোর্ট ভর্তি উকিল পেয়াদা আরদালি সান্ত্রীর মাঝেও যেমন লিখেছেন ‘ওগো আমার নবীন শাখী, ছিলে তুমি কোন বিমানে,’ তেমনই স্নান করার সময় মাথায় জল ঢালতে ঢালতে লিখেছেন, ‘জল বলে, চল মোর সাথে চল।’ পাহাড়ী সান্যাল এ গানটি শিখেছিলেন স্বয়ং অতুলপ্রসাদের কাছে। ‘মানুষ অতুলপ্রসাদ’ বইয়ে তিনি লিখছেন, “যে গান শিখলাম তার প্রথম ছত্রটি হলো – ‘জল কহে চল মোর সাথে চল তোর আঁখিজল হবে না বিফল।’ গায়ক-গায়িকারা সকলেই গান ‘জল বলে চল।’ বইতে ছাপাও তাই আছে। কিন্তু আমার মতো যারা অতুলদার কাছ থেকে এ গানটি শিখেছি, তারা শিখেছিল ‘জল কহে চল।’” দিলীপকুমার রায় লিখেছেন, “কবি সুরকারের প্রাণ কবিত্বে বা সুরে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না। আমি বিলেত থেকে ফিরে এসে ১৯২৩ সালে একটি গান বাঁধি গজল সুরে। এ গানটি শুনে অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ হয়ে এই ছকে বাঁধেন তাঁর বিখ্যাত গান ‘কত গান হলো গাওয়া।’ কাজী নজরুলের একটি গান আমি প্রায়ই গাইতাম হিন্দুস্থানি কাজরী সুরে বাঁধা – এত জল ও কাজল চোখে, পাষাণী, আনলে বলো কে। কবি এই সুরে বাঁধলেন চমৎকার মিস্টিক সুরে গান ‘জল বলে চল।’ অতুলপ্রসাদ ছিলেন যাকে বলে একজন মানুষের মতো মানুষ। স্বধর্মে সুরকার, কবি, গুণি। স্বভাবে প্রেমিক, ভক্ত, জিজ্ঞাসু।” রাজীব বলেন, “অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দিলীপ রায়ের সম্পর্কটা অত্যন্ত গভীর, নিবিড় সম্পর্ক। তবুও অতুলপ্রসাদ কোথাও কোথাও দিলীপকুমারের গায়কি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। দিলীপকুমার সব গানই নিজের মতো করে গাইতেন। কিছুটা তান করে গাইতে পছন্দ করতেন তিনি। যে কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও গান নিয়ে তাঁর দ্বৈরথ তৈরি হয়েছিল। দিলীপকুমার রবীন্দ্রশতবর্ষে লাইভ রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন কিন্তু রেকর্ড করার অনুমতি পাননি।” এ পর্যায়ে পুনার হরিকৃষ্ণ মন্দিরে দিলীপকুমারের অতি বৃদ্ধ বয়সে গাওয়া অতুলপ্রসাদের গান ‘সবারে বাস্ রে ভালো’ রেকর্ড থেকে বাজিয়ে শোনানো হয়। এরপর এই একই গান সত্যজিৎ ঘরনি বিজয়া রায়ের কণ্ঠে অতি দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড থেকে বাজিয়ে শোনানো হয়।
রাজীব বলেন, “অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌয় এ সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। ব্যারিস্টার হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত সফল। মেয়েদের স্কুল করা, গানের স্কুল করা, বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করা এ সব কাজে তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না। তিনি সবরকম কাজের একদম কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের ভাতখণ্ডে মিউজিক কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও তিনি আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ছিলেন। জুবিলি স্কুলের একরকম প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন তিনি। লক্ষ্ণৌয় এর যে রাস্তায় ছিল তার বাড়ি, সেটি তাঁর জীবদ্দশাতেই সরকারিভাবে তাঁর নামে নামকরণ করা হয়। মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে গুণগ্রাহীগন লক্ষ্ণৌ-এ তাঁর মর্মরমূর্তি স্থাপন করেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নামে একটি হল আছে সেখানে। গোখেলের অনুবর্তীরূপে তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। পরে লিবারেল ফেডারেশন বা উদারনীতিক সংঘভুক্ত হন এবং এর বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর উপার্জিত অর্থের বৃহৎ অংশ জীবিতকালেই লোকসেবায় ব্যয় হয়। অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকাংশ, তাঁর আবাসগৃহ ও গ্রন্থসত্বও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করে গিয়েছেন।
“অতুলপ্রসাদ ১৯৩২ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড থেকে দুটি গান নিজ কণ্ঠে রেকর্ড করেছিলেন। ১৯৩২ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতায়। এইচএমভির পরে বাঙালি উদ্যোগে যে দুটো রেকর্ড কোম্পানি তৈরি হয়েছিল কোলকাতায় সেগুলো হচ্ছে হিন্দুস্থান রেকর্ড ও মেগাফোন। হিন্দুস্থান রেকর্ডের প্রথম রেকর্ড রবীন্দ্রনাথের। এইচ টু নাম্বারের দ্বিতীয় রেকর্ডটি অতুলপ্রসাদের। আর তৃতীয় রেকর্ড রেনুকা দাশগুপ্তের, অতুলপ্রসাদের বোন সম্পর্কে।” এ পর্যায়ে অতুলপ্রসাদের রেকর্ডকৃত দুটো গান – ‘জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণী’ ও ‘মিছে তুই ভাবিস মন’ এবং রেনুকা দাশগুপ্তের গাওয়া ‘পাগলা মনটারে তুই বাঁধ’ ও ‘যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো সখী গো’- এই ৪টি গানের কিছু অংশ পরপর রেকর্ড থেকে বাজিয়ে শোনানো হয়। উল্লেখ্য, ‘জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণী’ গানটি ধ্রæপদ ও কীর্তনের অপূর্ব সংমিশ্রণ। তিলক-কামোদ রাগে বাঁধা এ গানটির সঞ্চারীতে কীর্তনাঙ্গের সুর।
শুক্লার নবম পরিবেশনা ছিল পিলু-সাওয়ানিতে বাঁধা ‘শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে।’ এরপর শুক্লা ‘মধুকালে এলো হোলি’ গেয়ে শোনান। এ গানটি কাফি-সিন্ধুতে রচিত, হিন্দুস্থানি কাফি ও খাম্বাজের ঢং এ বাঁধা। দিলীপকুমার রায় বলেছেন, “অতুলপ্রসাদের হিন্দুস্থানি ঢঙে বাঁধা কিছু গানে বাঙালি হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের রসও অনেকটা পাবেন। যেমন শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে, মধুকালে এলো হোলি ইত্যাদি।” শুক্লার একাদশ পরিবেশনা ছিল – একা মোর গানের তরী। এরপর তিনি ‘ওরে বন তোর বিজনে সঙ্গোপনে কোন উদাসী থাকে’ গানটি গেয়ে শোনান। দিলীপকুমার রায় বলেছেন, অন্যরা শুধু বাউল বা শুধু কীর্তন করেছেন কিন্তু অতুলপ্রসাদ এদের মিশ্রণও ঘটিয়েছেন সার্থকভাবে। যেমন বাউল-কীর্তন – মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে, যদি তোর হৃদযমুনা; মিশ্র বাউল কীর্তন – আর কত কাল থাকব বসে দুয়ার খুলে ইত্যাদি। দিলীপ কুমারের মতে অতুলপ্রসাদের গানগুলিকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়। এক, খাঁটি কীর্তন ও বাউলের সরল হৃদয়স্পর্শী সুরের সাথে তাঁর কবিত্বের আধুনিকতাকে স্বাভাবিকভাবে মেশানো হয়েছে, এখানেই অতুলপ্রসাদের সুন্দর মৌলিকতা। তাঁর আরেক কৃতিত্ব যে, এসব গানে হিন্দুস্থানী ঢঙকেও মেশাতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন কীর্তন-বাউলের সঙ্গে হিন্দস্থানি পিলুর রস দিয়ে ‘ওগো আমার নবীন শাখী, ছিলে তুমি কোন বিমানে’ তৈরি হয়েছে। আবার তিনি খাঁটি কীর্তনকে আধুনিক করে তুলেছেন, যেমন ‘কত কাল রবে নিজ যশ-বিভব’ ইত্যাদি।
রাজীব বলেন, সাহানা দেবী অতুলপ্রসাদের গানের অন্যতম কাণ্ডারী। তিনি অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে ‘সুরের খেয়া’য় লিখেছেন, “মৃদু মধুর সুরের নানা কাজের আলো-ছায়ার ভিতর ছোট্ট এক-একটি খোঁচ ও এক-একটি মোচড়ের ভিতর তাঁর সঙ্গীতে ধরা পড়ে সূ²তার স্পর্শ, রস, কমনীয়তা ও লালিত্য। সব জড়িয়ে তাঁর গান হয়ে ওঠে একটা ‘ডেলিকেসি।’ তাই হলো অতুলদার গানের বিশেষত্ব, নিজস্ব ছাপ, স্বকীয়তার ধরন। তাঁর সঙ্গীতে আছে পেলব মাধুর্যের স্নিগ্ধতায় ভরা মনোহরা স্পর্শ সব।” উল্লেখ্য, সাহানা দেবী অতুলপ্রসাদের গানের গায়কি নিয়েও বিস্তারিত লিখেছেন নানান সময়।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশের জন্মের সাথে জড়িয়ে আছে যে ভাষার প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নের সঙ্গে যেই গান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল একেবারে শুরু থেকেই, সেই গান – মোদের গরব মোদের আশা – কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের বাবা অতুলপ্রসাদের গানের অন্যতম কাণ্ডারী হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রেকর্ড থেকে বাজিয়ে শোনানো হয়। এ গানে হরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন ছবি দত্ত। এরপর শোনানো হয় সতী দেবী, কনক দাশ, অজয় বিশ্বাস ও সোমেন গুপ্তর কণ্ঠে রেকর্ডকৃত অতুলপ্রসাদের গান – বলো বলো বলো সবে শতবীণা বেণু রবে। এই রেকর্ডের পরিচালক সুরসাগর হিমাংশু কুমার দত্ত। সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর সম্পর্ক ছিল, যা নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না।
এ পর্যায়ে শুক্লা পরিবেশন করেন ভৈরবী রাগে স্বল্পশ্রæত একটি অতুলপ্রসাদের গান – তব অন্তর এত মন্থর। এরপর শুক্লা এ আসরে তাঁর সবশেষ গান ভৈরবী রাগে ‘আবার তুই বাঁধবি বাসা’ গেয়ে শোনান।
১৮৯৭-এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের প্রথম পরিচয় এবং সে সম্পর্ক আমৃত্যু দুজনে লালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পরিশেষ’ বইটি অতুলপ্রসাদকে উৎসর্গ করেন। ১৯১৪ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ হিমালয় ভ্রমণ সেরে রামগড়ে এসেছেন। সেখানে তাঁর কেনা বাড়ি ‘হৈমন্তী’তে অনেক আত্মীয়-পরিজন তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন। তবু তৃষ্ণার্ত কবি অতুলকে লিখলেন, “গ্রীষ্মের আতিশয্যে সকলেই মেঘের জন্য লালায়িত। আমি ভাবিতেছি অতুল কবে আসিয়া আমাদিগকে স্নিগ্ধ করিবেন।” কবির আমন্ত্রণে আপ্লুত অতুল লক্ষ্ণৌ থেকে ছুটে গেলেন। সেখানে তখন দিনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথও রয়েছেন। একদিন সূর্যোদয়ের আগেই ঊষালগ্নে একটি পাথরের উপর বসে রবীন্দ্রনাথ হিমালয়ের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে গুনগুন করে গাইছেন ‘এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে, সুন্দর।’ অতুলপ্রসাদ আড়াল থেকে সেই অবিস্মরণীয় গীত রচনা ও সুরসৃষ্টির সাক্ষী থাকলেন। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদকে নিয়ে কবিতা-গান লিখেছেন, অতুলপ্রসাদও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে।
অমল হোম অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে লিখেছেন, “সা¤প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত মানুষ রাজনীতিতে বিরল। যেদিন লক্ষ্ণৌয় এ হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট নিষ্পত্তি হলো, সেদিন তাঁর কী আনন্দ! আবার লক্ষ্ণৌতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হলে তিনি সেখানে ছুটে গেছেন। ফিরে এসে সেদিনই লিখেছেন, ‘পরের শিকল ভাঙিস পরে, নিজের নিগড় ভাঙরে ভাই।’ রামপ্রসাদী মালসী সুরে তাঁর গান ‘দেখ্ মা, এবার দুয়ার খুলে’ হিন্দু মুসলমানের মিলনের উপলক্ষে রচিত।” অতুলপ্রসাদের মরদেহ কাঁধে তুলে নিয়েছেন মহম্মদ নাসিম, জগৎনারায়ণ মোল্লা, মিস্টার টমাস, বিশ্বেশ্বর শ্রীবাস্তব ও আরো সকলে। এমন স¤প্রীতির ছবি আজকের ভারতে বিরল।
রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখেছেন, “অতুলপ্রসাদের সমগ্র রচনা পরিক্রমা করে উপলব্ধি করা যায় যে তিনি এমন একটি স্তরে এসেছিলেন যেখানে শিল্পী একটি সার্থক চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তখন একটা বোধ মনকে জাগ্রত করে যার ইঙ্গিতে শিল্পীর সমগ্র সৃষ্টি সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, গভীরতায়, মানবিকতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। খুব কম সঙ্গীতশিল্পীই এই স্তরে উন্নীত হতে পারেন।
আমাদের সঙ্গীতজগতে যে স্বল্প কয়েকজন এই দিব্য অনুভূতির স্পর্শলাভ করে পুণ্যশ্লোক বলে পরিগণিত হয়েছিলেন, অতুলপ্রসাদ তাঁদেরই একজন।ৃঅতএব আমরা দেখি, প্রচলিত লৌকিক রীতির ধারাকে অতুলপ্রসাদ উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের স্পর্শমাধুর্যে একটি বিশেষ আঙ্গিক দান করেছিলেন যার ফলে বাংলা সঙ্গীত সম্ভার অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। যেমন, লাউনিতে ‘কেন এলে মোর ঘরে,’ সাওয়ানিতে ‘ঝরিছে ঝর ঝর,’ পিলু-বারোয়াঁয় ‘কে আবার বাজায় বাঁশি,’ কাজরি ঢঙে ‘জল বলে চল, মোর সাথে চল’ প্রভৃতি। খাম্বাজের পরেই তাঁর পছন্দের রাগ ‘ভৈরবী’। ‘সে ডাকে আমারে’ এই রাগে বিখ্যাত গান। তাঁর ‘ভৈরবী’ বড় করুণ-মধুর! কিছু স্বল্প-প্রচলিত রাগেও তাঁর গান আছে, যেমন মেঘ, পঞ্চম, নট-নারায়ণ, নায়কী, কানাড়া, কর্ণাটী, খট্ ইত্যাদি; ‘তব পারে যাব কেমনে’ (নায়কী কানাড়া)। তাঁর গজল ছিল ভারি মরমী। ‘কত গান তো হল গাওয়া’, ‘ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে’ অথবা ‘ওগো ক্রন্দসী পথচারিণী,’ কীর্তনাঙ্গে ‘আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়,’ ‘ওগো সাথী মম সাথী’, ‘কতকাল রবে যশ-বিভব অন্বেষণে’ বা ‘যদি তোর হৃদযমুনা।’ বাউল সুরে ‘মন রে আমার শুধু তুই বেয়ে যা দাঁড়,’ ‘আর কতকাল থাকব বসে,’ ‘মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে,’ ‘প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল’ বা ‘মোদের গরব, মোদের আশা’ গানগুলি। অতুলপ্রসাদের ধ্রুপদাঙ্গের গান খুব কম। ইমনকল্যাণে ‘নমো বাণী বীণাপাণি’ একটি খাঁটি ধ্রুপদ। আর ‘ক্ষমিও হে শিব’ গানটিও ধ্রুপদ আঙ্গিকের।”
অতুলপ্রসাদী গান শিল্পী ইলোরা আহমেদ শুক্লার অত্যন্ত সমাহিত, পরিমিত, নিয়ন্ত্রিত ও দরদী পরিবেশনায় দর্শক-শ্রোতারা মুগ্ধ হন। রাজীব চক্রবর্তীর গবেষণালব্ধ ও আন্তরিক আলোচনা এবং আর্কাইভ থেকে অতি দুর্লভ বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক গানের নমুনা উপস্থাপন সবাইকে মুগ্ধ করে। দর্শক-শ্রোতা পুরোটা সময় উপভোগ করেছেন এবং মন্তব্য করে সক্রিয় থেকেছেন। সামগ্রিকভাবে অতুলপ্রসাদ সেনের জীবন ও সঙ্গীত নিয়ে আলোচক রাজীব চক্রবর্তীর আলোচনা এবং শিল্পী ইলোরা আহমেদ শুক্লার সংগীত পরিবেশনায়, সত্যিকার অর্থেই সার্ধশত জন্মবর্ষে এক পূর্ণাঙ্গ অতুলপ্রসাদ সেনকে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে কিছুটা হলেও? অতুলপ্রসাদ সেনের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিবেদিত পাঠশালার এ আসরের সঞ্চালনায় ছিলেন ফারহানা আজিম শিউলী।